ডা. হেলাল উদ্দিন আহমেদ
সহযোগী অধ্যাপক,
চাইল্ড অ্যাডোলেসেন্ট অ্যান্ড ফ্যামিলি সাইকিয়াট্রি,
জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট।
বৈষম্য, বঞ্চনা, হতাশা, মানসিক রোগ, মাদকাসক্তি এবং না পাওয়ার যন্ত্রণায় জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা থেকে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় মানুষ। মহামারীর মতোই বাড়ছে এ প্রবণতা। এ থেকে মানুষকে সচেতন করার লক্ষ্যে ২০০৩ সাল থেকে প্রতি বছর ১০ সেপ্টেম্বর বিশ্বব্যাপী পালিত হয়ে আসছে আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস।
এ বছর আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে, ‘কাজের মাঝে জাগাই আশা।’ অর্থাৎ কেবল সচেতনতাই নয়, বরং আত্মহত্যা প্রতিরোধে আমাদেরকে সক্রিয় হতে হবে এবং কাজ করতে হবে।
বিশ্বে আত্মহত্যার প্রবণতা বেড়েই চলেছে। বিশেষ করে ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি। বিশ্বে এ বয়সীদের মৃত্যুর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ কারণ আত্মহত্যা আর প্রথম হলো সড়ক দুর্ঘটনা।
যেসব কারণে বিপর্যয়
আত্মহত্যার কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক, মেডিকেলিক্যাল, আইনগত ও পারস্পারিক সম্পর্ক ইত্যাদি। খুব তাত্ত্বিক আলোচনায় যাবো না। যদি আমাদের (মেডিকেল) জায়গা থেকে বলি, তাহলে বলতে হবে—প্রথমত একটি সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন হচ্ছে। এটা সারাপৃথিবীতেই হচ্ছে। রেপিড আরবানাইজেশন, ইমিগ্রেশন ও মাইগ্রেশন হচ্ছে। মানুষ কাজের সন্ধানে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাচ্ছে; আর এর মধ্যে তাদের মানসিক অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে। মনের উপর টানাপোড়েন পড়ছে, মানসিক চাপ বাড়ছে এবং অনেক সময় এই চাপ বা কষ্ট থেকে মুক্তি পেতে মানুষ আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়, যা হয়তো ভুল। এটি আত্মহত্যার একটি সমাজতাত্ত্বিক কারণ। এ ছাড়া সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে অনেকের অনেক সময় নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে বেগ পেতে হয়। ফলে আত্মহত্যা করে।
গবেষণাগুলো থেকে প্রমাণিত—পৃথিবীর সকল আত্মহত্যার পেছনেই আত্মহত্যাকালীন ব্যক্তির মানসিক অবস্থার অবনতি ছিল। অর্থাৎ বিষণ্ণতা, ব্যক্তিত্বের বিকার, সিজোফ্রেনিয়া, মুড ডিসঅর্ডার, মাদকাসক্তি ইত্যাদিতে মানসিক রোগে তিনি ভুগছিলেন। আর এ কারণেই মানুষ আত্মহত্যা করে থাকে। এ ছাড়া এই রোগগুলোর প্রতি এক ধরনের বদমান জড়িয়ে আছে, যার ফলে সংকোচের কারণে আমরা এগুলোর চিকিৎসা করতে সচেষ্ট হই না, উৎসাহিত হই না। সেটাও আত্মহত্যার অন্যতম একটি কারণ।
দেশে প্রতি লাখে ৬ আত্মহত্যা


বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গবেষণা অনুযায়ী, বাংলাদেশে প্রতি বছর ১ লাখ মানুষের মধ্যে ৫.৯ জন অর্থাৎ ১ লাখ মানুষের মধ্যে ছয়জন আত্মহত্যা করে থাকে। আমাদের পুলিশ বিভাগের রিপোর্ট অনুযায়ী, বছরে গড়ে ১০ থেকে ১১ হাজার মানুষ আত্মহত্যা করে থাকে। সে হিসাবে, দেশে দিনে প্রায় ২৮টি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে। গবেষণা সংস্থা আঁচল ফাউন্ডেশনের তথ্য অনুযায়ী, এই করোনাকালে ২০২০ সালের মার্চ থেকে ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ পর্যন্ত সময়ে প্রায় ১৪ হাজার মানুষ আত্মহত্যা করেছে। বিভিন্ন পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই হচ্ছে আমাদের দেশে আত্মহত্যার হিসাব।
দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোর তুলনায়, আমাদের দেশে আত্মহত্যার হার কম। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী, দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় প্রতি লাখে প্রায় ১৩ জন আত্মহত্যা করে। এর বিপরীতে আমাদের দেশে প্রতি লাখে আত্মহত্যা করছে ছয়জন। এদিক থেকে আমরা খানিকটা ভালো অবস্থানে আছি।
তুলনামূলক বিশ্লেষণে কম মনে হলেও আমাদের দেশেও প্রতিনিয়ত আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ছে। আমাদের দেশে বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, দেশে আত্মহত্যায় প্রাণ হারানোদের বেশিরভাগই নারী। অর্থাৎ এখানে আত্মহত্যায় মারা যায়, তাদের দুই-তৃতীয়াংশই নারী, তাদের বেশিরভাগেরই বয়স ১৫ থেকে ৩০ বছর।
নারীদের বেশি আত্মহত্যার কারণ
এর কারণ পুরুষের চেয়ে নারীদের মধ্যে বিষণ্নতার হার দ্বিগুণ। আর বিষণ্নতা হলো আত্মহত্যার অন্যতম একটি কারণ। সরকার নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণ এবং শিক্ষা প্রসারে অনেক চেষ্টা করলেও এখানে দীর্ঘদিনের একটি ঘাটতি রয়ে গেছে। এখনও নারীর জন্য ঘরে-বাইরে স্বাবলম্বী হয়ে উঠার মতো পরিবেশ নিশ্চিত করা যায়নি। তার সাধিকার, নিজের মতো করে চিন্তা করার জায়গাটি তৈরি করা যায়নি। আর এটি মাঝে মাঝে তাকে বিপন্ন করে, বিপর্যস্ত করে। এটিও আত্মহত্যার অন্যতম কারণ। আর ক্ষুদ্র পরিসরে চিন্তা করলে দেখা যাবে, প্রেম ও পরীক্ষায় ব্যর্থতা, যৌতুক ও পারিবারিক সহিংসতা—এসব কারণে নারীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি কাজ করে।
সীমান্তবর্তী ও দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে আত্মহত্যা বেশি
উপকরণের সহজপ্রাপ্যতার কারণে সীমান্তবর্তী ও দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে অপেক্ষাকৃত বেশি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে। সেটি ভৌগলিক কোনো কারণে হচ্ছে, বিষয়টি এমন নয়। এর পেছনে কতগুলো কারণ রয়েছে, যেমন: এসব অঞ্চলে আত্মহত্যার উপকরণের সহজপ্রাপ্যতা। অঞ্চলগুলো মূলত কৃষিপ্রধান, সেখানে দুই ফসলি বা তিন ফসলি জমি রয়েছে আর এ কারণে প্রতিটি ঘরে কীটনাশক মজুদ থাকে। ফলে আত্মহত্যার উপকরণের সহজপ্রাপ্যতা রয়েছে সেখানে। দ্বিতীয়ত: একজন মানুষ যখন আত্মহত্যা করে, তখন আশপাশের মানুষ এটাকে অবজারভেশনাল লার্নিং হিসেবে নেয় অর্থাৎ দেখে দেখে তারাও শিখে। আর এই কারণে এসব অঞ্চলে আত্মহত্যার প্রবণতা বেড়ে যেতে পারে।
সুতরাং আত্মহত্যা উপকরণের সহজপ্রাপ্যতা দূর করতে হবে। কীটনাশক যথাযোগ্য জায়গায় রাখতে হবে, তালাবদ্ধ করে রাখতে হবে। যত্রতত্র কীটনাশক বিক্রি করা চলবে না। প্রেসক্রিপশন ছাড়া ঘুমের ওষুধ, বিশেষ করে আত্মহত্যা করার মতো ওষুধ বিক্রি করার জায়গাটি আমাদের সক্রিয়ভাবে বন্ধ করতে হবে।


আত্মহত্যা প্রতিরোধ করতে হবে
আরেকটি বিষয়: যারা আত্মহত্যা করবেন, তারা মূলত আগে থেকেই আত্মহত্যার ইঙ্গিত দিয়ে থাকেন। এটি তারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, আড্ডায় কথাবার্তায় দিয়ে থাকেন। সেই ইঙ্গিতগুলো আমাদের বুঝতে হবে। বুঝতে পারলে সে সময় তাদেরকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করা যাবে না। অর্থাৎ তাকে বলা যাবে না তুমি মরতে চাও, …মরবা না; আত্মহত্যার কথা যে বলে সে মরে না। এই ধরনের কথাগুলো তাকে কখনোই বলা যাবে না। আত্মহত্যার প্রতিটি ইচ্ছাকে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে তা আমাদের প্রতিরোধ করতে হবে। যে আত্মহত্যার কথা বলে, চেষ্টা করতে হবে তাকে ওই চিন্তা থেকে ফিরিয়ে আনতে।
খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, মানসিক রোগের যথাযথ চিকিৎসা ব্যবস্থা করতে হবে। এ কারণেই বেশিরভাগ আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে। আমরা বরাবরই মানসিক রোগের চিকিৎসা করতে অনেকটা উদাসীন। আর মানসিক রোগের ওষুধ খেতে আরো বেশি উদাসীন। আত্মহত্যা প্রতিরোধ করতে হলে মানসিক রোগের ওষুধ সেবন করতে হবে। ওষুধকে ভয় পাওয়া যাবে না, জুজুর ভয় দেখানো যাবে না। পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার ভয়ে ওষুধ বন্ধ রাখা যাবে না।
কারও মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা থাকলেও ওষুধ সেবন করতে হবে, ওষুধ সেবন ছাড়া এটা প্রতিরোধ করা সম্ভব না।
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কঠোর নিয়ম-নীতি থাকলে, সেটা ছাত্রবান্ধব করতে হবে। সেখানে শারীরিক শাস্তি থাকবে না, কাউকে আঘাত করবে না, শারীরিক নির্যাতন থাকবে না। ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, উত্তপ্ত ইত্যাদি বন্ধ করতে হবে। পরীক্ষার ফলাফলকে এমন একটি সহনশীল প্রর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে, যাতে এটাকে তারা জীবনের অংশ মনে করে। পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়াকে তারা যেন পাঠ্যক্রমের অংশ হিসেবে নেয়। প্রয়োজনে ব্যর্থতাকে মাঝে মাঝে উদযাপন করতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষকদেরকে সবার আগে সচেতন হতে হবে। কারও মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা দিলে সহপাঠীদের তৎক্ষণাৎ তার প্রতি সহযোগী হতে হবে, সমানুভূতি প্রদর্শন করতে হবে এবং তাকে নিয়ে আসতে হবে চিকিৎসার আওতায়।
আর পরিবারের ভূমিকা হবে—কোন ছাত্রকে লক্ষ্য নির্ধারণ করে দেওয়া যাবে না, যে তোমাকে জিপিএ-৫ পেতেই হবে; এটা না করলে আমি মুখ দেখাবো কেমন করে? তোমাকে অমুখ জায়গায় চান্স পেতেই হবে। এ ধরনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে দেওয়া যাবে না।




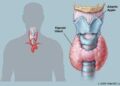

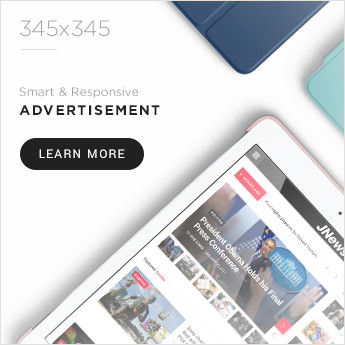




Discussion about this post